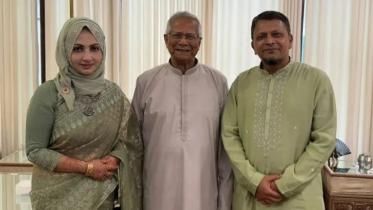জিও-পলিটিকস (Geopolitics) বলতে বোঝানো হয়—একটি রাষ্ট্র বা অঞ্চলের ভূ-অবস্থান, ভূ-প্রাকৃতিক সম্পদ, সামরিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপথ ও প্রভাবের বিশ্লেষণ। সহজভাবে বললে, ভূগোল ও রাজনীতির সংমিশ্রণে যে কৌশলগত চিন্তা ও ক্ষমতার খেলা গড়ে ওঠে মোটাদাগে তাই হচ্ছে জিও-পলিটিকস।
Geopolitics শব্দটি এসেছে “Geo” (ভূগোল) ও “Politics” (রাজনীতি) শব্দ থেকে। এটি বোঝায় কিভাবে একটি দেশের ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা—এই সবকিছুর সমন্বয়ে তার আন্তর্জাতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়।
সুতরাং জিও-পলিটিকস হলো এক প্রকার ক্ষমতার খেলা, যেখানে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সামরিক-অর্থনৈতিক গুরুত্ব কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখে। অনেক সময় দেশগুলো এ খেলার শিকার হয়, আবার কেউ কেউ খেলোয়াড় হিসেবে অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।“যে দেশটির ভূগোল কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সে দেশটির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঝুঁকিতে পড়ে।”
জিও পলিটিকসের মূল উপাদান:
ক. ভূ-অবস্থান (Geographical location): কোন দেশ কোথায় অবস্থিত—এই তথ্যই অনেক সময় তার কৌশলগত গুরুত্ব নির্ধারণ করে।
খ. প্রাকৃতিক সম্পদ: তেল, গ্যাস, পানি, খনিজ ইত্যাদি সম্পদের দখল ও নিয়ন্ত্রণ একটি বড় জিও-পলিটিক্যাল ফ্যাক্টর।
গ. সামরিক শক্তি ও জোট: দেশটি কাদের বন্ধু, কাদের প্রতিপক্ষ—এই সামরিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক।
ঘ. অর্থনৈতিক রুট: বন্দর, করিডর, বাণিজ্য পথ, চীন-ভারতের Belt and Road Initiative-এর মতো প্রকল্পগুলো।
ঙ. ধর্ম, জাতিসত্তা, সংস্কৃতি: কখনও এগুলো ব্যবহার হয় জিও-পলিটিক্যাল চাপ বা অস্থিরতা তৈরির হাতিয়ার হিসেবে।
জিও পলিটিকস কেনো গুরুত্বপূর্ণ:
ক. ক্ষমতা নির্ধারণে: কোন দেশ বিশ্বে কতটা প্রভাবশালী হবে, তা অনেকাংশে নির্ভর করে তার ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর।
খ. যুদ্ধ ও সংঘাতের কারণ: ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে দেশে দেশে যুদ্ধ বাধে। যেমন—ইরাক, আফগানিস্তান, ইউক্রেন।
গ. নিরাপত্তা নীতিতে প্রভাব: জিও-পলিটিক্যাল হুমকির কারণে অনেক দেশ সামরিক জোটে যোগ দেয় বা প্রতিরক্ষা জোরদার করে।
ঘ. অর্থনৈতিক রুট ও বাণিজ্য: জাহাজ চলাচলের পথ, করিডোর (সড়ক-পথ, রেলপথ) বা বন্দর দখল—সবই জিও-পলিটিকসের অংশ।
তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি:
এ ব্যাপারে Halford Mackinder বলেছেন, ইউরেশিয়ার “হৃদয়ভূমি” (Central Asia, Russia) যে নিয়ন্ত্রণ করবে, সে-ই বিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। এটিকে Heartland Theory বলা হয়। তাঁর মতে, Who rules East Europe commands the Heartland; who rules the Heartland commands the World Island; who rules the World Island commands the world. আরেক তাত্ত্বিক Nicholas Spykman বলেছেন, উপকূলবর্তী অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ (East Asia, South Asia, Middle East) বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর তত্ত্বকে Rimland Theory বলা হয়। আর ইউরোপীয় দার্শনিক কার্ল স্মিট Carl Schmitt ও Kritike ‘রাজনৈতিক ভূগোল’-এর ধারণায় বলেন, স্থান, সীমান্ত এবং শত্রু-পক্ষ চিহ্নিত করাই রাষ্ট্রের কৌশলগত অবস্থান নির্ধারণ করে।
জিও-পলিটিকসের শিকার যারা:
ক. আফগানিস্তান (দ্য গ্রেভইয়ার্ড অফ এম্পায়ারস):
আফগানিস্তান তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে “গ্রেট গেম”-এর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ১৯শ শতকে (ব্রিটিশ বনাম রাশিয়া)। ১৯৮০-এর দশকে সোভিয়েত হামলা এবং ২০০১-এর পর আমেরিকার হস্তক্ষেপ ছিল সরাসরি জিও-পলিটিক্যাল কৌশলের ফল।
এটি ছিল ব্রিটিশ ও রুশ সাম্রাজ্যের কৌশলগত দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু (“The Great Game”)।
সোভিয়েত আক্রমণ (১৯৭৯) ও আমেরিকান হস্তক্ষেপ (২০০১) ছিল মূলত: তেল-গ্যাসের করিডোর নিয়ন্ত্রণ। ইসলামি মৌলবাদের কৌশলগত দমন। রাশিয়া-চীন সীমান্তে প্রভাব বিস্তার। হাজারো নিরীহ মানুষের জীবন গেল, কিন্তু ক্ষমতাধর দেশগুলো তাদের ‘কৌশলগত লাভ’তাড়াতেই ব্যস্ত ছিল।
খ. ইরাক (তেলের রাজনীতি ও সাম্রাজ্যবাদ):
তেল-সমৃদ্ধ দেশ হওয়ায় আমেরিকার ২০০৩ সালের ইরাক আক্রমণের পেছনে একাধিক ভিন্নমত থাকলেও অনেক বিশ্লেষকের মতে এটি ছিল জিও-পলিটিক্যাল আগ্রহ থেকে উদ্ভুত। আমেরিকার ইরাক আক্রমণ ‘WMD’ (mass destruction অস্ত্র) বন্ধ করার অজুহাতে হলেও বাস্তবের কারণ ছিল-ইরাকের বিশাল তেল-ভান্ডার, মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার, ইরানকে ঘিরে রাখার পরিকল্পনা ও সাদ্দাম হোসেনকে সরিয়ে দিয়ে একধরনের রাজনৈতিক ‘re-engineering’ করা।
গ. ইউক্রেন-ন্যাটো বনাম রাশিয়া:
ইউক্রেনের ইউরোপের দিকে ঝুঁকে পড়া এবং রাশিয়ার কাছাকাছি অবস্থান জিও-পলিটিক্যাল দ্বন্দ্বকে তীব্র করেছে। ফলে ২০২২ সালে রাশিয়ার আক্রমণ এরই বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। ইউক্রেন চায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ন্যাটোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু রাশিয়া তা চায় না। কারণ: ইউক্রেন রাশিয়ার “buffer state” হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী বন্দর (সেভাস্তোপল, ওডেসা) সামরিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখল আর ২০২২ সালে পূর্ণ আক্রমণ-সবই ভূ-রাজনৈতিক খেলার অংশ মাত্র।
ঘ. প্যালেস্টাইন:
জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী ভূরাজনৈতিক (geopolitical) সংকটের শিকার হচ্ছে প্যালেস্টাইন। এই সংকট শুধু স্থানীয় বা ধর্মীয় কোনো দ্বন্দ্ব নয়—এটি আন্তর্জাতিক রাজনীতি, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, এবং বিশ্ব শক্তির আধিপত্য বিস্তারমূলক স্বার্থের গভীর প্রভাবের ফল। একটি ভূরাজনৈতিক “পাওয়ার গেম”-এর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে দেশটি। যেখানে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ, মুক্তি ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির স্বপ্ন বারবার চাপা পড়ে বিশ্বশক্তির স্বার্থে। এটি শুধু ধর্ম বা জাতিসত্তার লড়াই নয় বরং একটি বহুমাত্রিক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, যেখানে মানবতা বারংবার হার মেনেছে। উদাহরণস্বরূপ:
১. উপনিবেশবাদ ও ব্রিটিশ ভূমিকা:
১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণার (Balfour Declaration) কথা বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ সরকার এই ঘোষণার মাধ্যমে ইহুদি জনগণকে একটি “জাতীয় আবাসভূমি” প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয় প্যালেস্টাইনের মাটিতে। যেখানে তখন আরব মুসলিম ও খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এটি একটি সুস্পষ্ট জিওপলিটিকাল স্ট্র্যাটেজি ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক স্বার্থের অংশ—বিশ্বযুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যের তেলভিত্তিক কৌশলগত অবস্থানকে কাজে লাগাতে।
২. জাতিসংঘ বিভাজন পরিকল্পনা (1947): UN Partition Plan প্যালেস্টাইনকে দুটি রাষ্ট্রে ভাগ করার প্রস্তাব দেয়। একটি ইহুদি রাষ্ট্র ও একটি আরব রাষ্ট্র। ইহুদি পক্ষ এটি মেনে নিলেও আরব বিশ্ব এই পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে শুরু হয় ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ। এতে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হয়, কিন্তু প্যালেস্টাইনিদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন হয়নি। বহু মানুষ উচ্ছেদ ও উদ্বাস্তু হয়—একে বলা হয় Nakba (বিপর্যয়)।
৩. শীতল যুদ্ধ ও সুপার পাওয়ারের ভূমিকায় প্যালেস্টাইন: সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে প্যালেস্টাইন ইস্যুকে ব্যবহার করে। ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মিত্রে পরিণত হয়, আর প্যালেস্টাইনকে সমর্থন করে আরব দেশগুলো ও সোভিয়েত-ঘেঁষা জোট। এই মেরুকরণ প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও স্বাধীনতার পথ আরও জটিল করে তোলে।
৪. ইসরায়েল-আরব চুক্তি ও প্যালেস্টাইনের পশ্চাৎপসরণ: ১৯৭৯ সালের ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে মিশর ইসরায়েলের সাথে শান্তি চুক্তি করে। অনেক আরব দেশ নিজেদের স্বার্থে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে। এই অবস্থান প্যালেস্টাইনকে একপ্রকার কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতায় ফেলে।
৫. তেল রাজনীতি ও পশ্চিমা স্বার্থ: মধ্যপ্রাচ্য তেল-সমৃদ্ধ হওয়ায় পশ্চিমা দেশগুলো এখানকার রাজনীতিতে সক্রিয় হস্তক্ষেপ করে। ইসরায়েলকে শক্তিশালী মিত্র হিসেবে ধরে রাখার মাধ্যমে পশ্চিমা শক্তিগুলো তেলের রুট ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়। প্যালেস্টাইন ইস্যু অনেক সময় মানবাধিকার প্রশ্ন থেকে সরে গিয়ে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থে গৌণ হয়ে পড়ে।
৬. আধুনিক ভূরাজনীতি: আব্রাহাম অ্যাকর্ড ও মুসলিম বিশ্বের বিভাজন: ২০২০ সালে আব্রাহাম অ্যাকর্ড-এর মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কো প্রমুখ দেশ ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়, যা একসময় অকল্পনীয় ছিল। প্যালেস্টাইন প্রশ্ন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে “নেতৃত্বহীন ইস্যুতে” পরিণত হয়, যেখানে আরব দেশগুলো নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।
৭. মিডিয়া ও তথ্য যুদ্ধ: আধুনিক ভূরাজনীতিতে শুধু অস্ত্র নয়, তথ্য ও ভাবনার নিয়ন্ত্রণও একটি কৌশল। আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ইসরায়েলের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় বেশি গুরুত্ব পায়, আর প্যালেস্টাইনিদের প্রতিবাদকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়—যা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
৮. গাজা ও পশ্চিম তীর: বিভাজন ও নিয়ন্ত্রণ: প্যালেস্টাইনের দুটি অংশ—গাজা (হামাস কর্তৃক শাসিত) এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক (ফাতাহ ও প্যালেস্টাইন অথরিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত)—একই জাতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। ইসরায়েল ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো এই বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে প্যালেস্টাইনের জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করে।
সুতরাং ইসরায়েলের অবস্থান এবং পশ্চিমা বিশ্বের কৌশলগত সমর্থন একে একটি জিও-পলিটিক্যাল সংকটে পরিণত করেছে। ধর্মীয়, জাতিগত ও ভৌগোলিক দ্বন্দ্ব মিলিয়ে এটি রীতিমতো একটি জিও-পলিটিকসের কেস।
ঙ. প্রসঙ্গ যখন বাংলাদেশ:
ভারতের সাথে সম্পর্ক, চীন-ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সাউথ-এশিয়া গেটওয়ে হিসেবে বাংলাদেশ একটি জিও-পলিটিকসের চরম স্থানে রয়েছে। তিস্তা চুক্তি, রোহিঙ্গা সংকট, ট্রানজিট ইস্যু—সবই জিও-পলিটিকস দ্বারা প্রভাবিত। মোটাদাগে বাংলাদেশ হলো দক্ষিণ এশিয়ার Geo-strategic চাবিকাঠি। ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র — তিন পরাশক্তির মধ্যকার কৌশলগত দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে এক “Pivot Country” হয়ে উঠছে। এর অন্যতম কারণ: বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্ব, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের ব্যবহার, ভারতীয় উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রবেশদ্বার (Siliguri Corridor), চীনের Belt and Road Initiative এর একটি অংশ হওয়ার সম্ভাবনা
উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, তিস্তা চুক্তি বিলম্ব – ভারতের রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং চীনের তহবিল পরিকল্পনার প্রভাব বিদ্যমান। রোহিঙ্গা সংকটের গভীরে – মিয়ানমার, চীন, ভারত ও পশ্চিমা বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত।
গেল কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থান এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশটিকে একটি জটিল ও সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে ফেলেছে, যেখানে অভ্যন্তরীণ সংকট ও আন্তর্জাতিক চাপ একসাথে কাজ করেছে। ২০২৪ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং নোবেলবিজয়ী ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি সাংবিধানিক সংকটে পড়ে। এই সরকারকে অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক বলে সমালোচনা করা হয়েছে, এবং ২০২৬ সালের এপ্রিলের নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে ইউনুস সময়ক্ষেপণ করছেন বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিযোগ করেছে। বিএনপি ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলো এই বিলম্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, যা দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে ভারতের ঘনিষ্ঠ মিত্র হলেও, সাম্প্রতিক সময়ে চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার করেছে। এই পরিবর্তন ভারতের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে সীমান্ত নিরাপত্তা, পানি বণ্টন (যেমন তিস্তা নদীর পানি ভাগাভাগি) এবং বাণিজ্যিক নির্ভরতার ক্ষেত্রে ।
মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমন বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সীমান্ত লঙ্ঘন এবং সেন্ট মার্টিন দ্বীপের কাছে গোলাবর্ষণের ঘটনা বাংলাদেশের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে ।
২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ২,৫০০-এর বেশি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং ৭০০-এর বেশি গুমের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিশেষায়িতবাহিনী র্যাব এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যা দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছে । তাছাড়া শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি অপসারণ এবং তার ছবি মুদ্রা থেকে বাদ দেওয়ার মতো পদক্ষেপগুলো বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয় ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এই ধরনের পদক্ষেপ দেশটির অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান।
সুতরাং বর্তমানে বাংলাদেশ জটিল এক ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি, যেখানে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক, মানবাধিকার ইস্যু এবং জাতীয় পরিচয়ের সংকট একসাথে কাজ করছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন, মানবাধিকার রক্ষা, এবং ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ অপরিহার্য।
অতএব বলা যেতেই পারে-জিও-পলিটিকস ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে একেবারেই নঞর্থক। এটি মোটেও নৈতিক নয় বরং ক্ষমতার খেলা। যেখানে শক্তিশালী দেশগুলো দুর্বল দেশগুলোকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে। সাধারণ জনগণ যেখানে হয় যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, শরণার্থী সংকট ও দারিদ্র্যের শিকার। ভবিষ্যতের জিও-পলিটিক্সের ধরণ চেঞ্জ হওয়ায় এটি আরও ভয়ঙ্কর গতে পারে। যেমন তা হতে পারে Climate Geopolitics. যেখানে পানির উৎস ও জলবায়ু পরিবর্তন—আগামী দিনে যুদ্ধের কারণ হতে পারে। Cyber Geopolitics তথা তথ্য-প্রযুক্তি ও তথ্য-নিয়ন্ত্রণ (5G, TikTok, surveillance)। Space Geopolitics তথা চাঁদ বা মহাকাশ দখলও পরবর্তী স্তরের কৌশল বলে গণ্য হবে।
এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে ঘিরে চীন-ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। যার ছায়া প্রচ্ছায়া পড়েছে জিও-পলিটিকটিকসের ওপর। বাংলাদেশের কপাল পুড়েছে তার
ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে। দেশটির ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের অন্যতম কারণ হলো-ভারতীয় উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর প্রবেশপথ তথা শিলিগুড়ি করিডোরের অদূরে বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগর ঘেঁষা উপকূলীয় অঞ্চল, যা সামরিক ও নৌ-বাণিজ্যিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এশিয়ার ‘নিউ লজিস্টিক হাব’ হওয়ার সম্ভাবনা চট্টগ্রাম ও পায়রা বন্দর। আঞ্চলিক সংযোগ (Connectivity Hub) ইস্যুটিও সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। চীন চায় এই অঞ্চলকে তার Belt and Road Initiative (BRI)-এর অংশ করতে। পক্ষান্তরে ভারত চায় BBIN (Bangladesh-Bhutan-India-Nepal) কানেকটিভিটি জোরদার করতে। আর এই দুই রাষ্ট্রের ফাঁক গলিয়ে যুক্তরাষ্ট্র চায় Indo-Pacific Strategy-এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকাকে কাজে লাগাতে।
বাংলাদেশে চীন যেভাবে ফ্যাক্টর:
চীনের আগ্রহ BRI & Maritime Silk Road-এ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি। পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা- “String of Pearls” স্ট্র্যাটেজির অংশ। ভারতকে ঘিরে রাখা — নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ মিলে একপ্রকার জিও-পলিটিক্যাল ব্যালেন্সিং।
বাংলাদেশের জিও পলিটিকসে মাথা ঘামাতে গিয়ে চীন পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন ও নির্মাণ (CREC) করেছে। করেছে পায়রা ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন পরিকল্পনা। এছাড়া চীনের সাথে সামরিক সহায়তা ও সরঞ্জাম বিক্রয় (Submarine deal) ও জীবাণু যুদ্ধ, AI surveillance, এবং Huawei প্রযুক্তি নিয়েও আগ্রহ বাড়িয়েছে। আর এতে যে ঝুঁকি রয়েছে তা হলো- ঋণের ফাঁদের আশঙ্কা (Debt-trap diplomacy). শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দর এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যপক্ষে, চীনের প্রভাব বৃদ্ধি হলে ভারতের উদ্বেগ ও পশ্চিমাদের চাপও যথেষ্ট পরিলক্ষিত বটে।
ভারত যে চোখে দেখে বাংলাদেশকে:
চীনের মতো ভারতেরও আগ্রহ বহুমাত্রিক। নিজস্ব উত্তর-পূর্ব রাজ্যে প্রবেশাধিকার (via transit) ও চীনের প্রভাববলয়ে বাংলাদেশকে ঢুকতে না দেয়া। সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা, সীমান্ত নিরাপত্তা ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকানোও তাদের গভীর আগ্রহের জায়গা। পাশাপাশি অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন (তিস্তা, গঙ্গা) ইস্যু নিয়ন্ত্রণেও দেশটির আগ্রহ যথেষ্ট। এব্যাপারে ভারতের পদক্ষেপ হলো ট্রানজিট সুবিধা, রেল-সড়ক উন্নয়ন, লাইনের অফ ক্রেডিট (LOC) ও বাণিজ্য বৃদ্ধি, নাথুরাম-শিলিগুড়ি করিডোরে নিরাপত্তা চুক্তি, সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো (BSF নির্মমতা নিয়ে বিতর্কও আছে)।
যদিও বাংলাদেশে ভারতের অতিরিক্ত প্রভাব নিয়ে জনমনে ক্ষোভ রয়েছে। বর্তমান সময়ে পদে পদে যার খেসারত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিস্তা চুক্তির বিলম্বে চীনের জন্য পথ খুলে যাওয়া, হিন্দুত্ববাদ এবং “NRC-CAA” ইস্যুতে জনমনে সন্দেহ ও আতঙ্ক।
আমেরিকা কোন দৃষ্টিতে দেখে বাংলাদেশকে:
ভারত ও চীনের মতো যুক্তরাষ্ট্রেরও মোটা দাগে এক ডজন উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা চায় ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব ঠেকানো, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র ইস্যুতে প্রভাব খাটানো, রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে কৌশলগত হস্তক্ষেপ করতে চাইছে। এ সবের পদক্ষেপ হিসেবে দেশটি যা করেছে তা হলো ভিসা নীতির হুমকি ও বাস্তবায়ন (Democracy Visa Policy), QUAD সহযোগিতা প্রসঙ্গে বাংলাদেশকে কাছাকাছি আনার চেষ্টা, নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক নজরদারি সহযোগিতা (Bay of Bengal Initiative)। এসব নিয়ে যে অভিযোগ রয়েছে তা হলো চাপ দিয়ে কূটনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার, গণতন্ত্রের নামে রাজনৈতিক ভারসাম্যে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ও সম্ভাব্য “কান্টেইনমেন্ট স্ট্র্যাটেজি”-তে বাংলাদেশ জড়িয়ে পড়া।
এভাবে তিন পরাশক্তির টানাটানিতে দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি। অর্থনৈতিক ঋণ ও বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে এ কারণে। সবাইকে বিশ্বাস করতে গিয়ে সবারই বিশ্বাস ভঙ্গের মতো অনেকটা। তাই রাজনৈতিক অস্থিরতা ব্যবহারের চেষ্টা রয়েছে বিদেশি শক্তির। এমনকি রোহিঙ্গা সংকটকে আন্তর্জাতিক জিও-পলিটিক্যাল খেলা হিসেবে ব্যবহারও চলছে।
সুতরাং জিও-পলিটিকস এমন এক বাস্তবতা যা কোনো দেশের পক্ষেই এড়ানো সম্ভব নয়। এটি কখনও আশীর্বাদ—যদি কৌশলগত অবস্থানকে কাজে লাগাতে পারে। আবার কখনও অভিশাপ—যদি দেশটি বড় শক্তিগুলোর খেলার বোর্ডে একপাশের ঘুঁটি হয়ে দাঁড়ায়। তাই বাংলাদেশের মতো ছোট ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচিত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি, স্মার্ট কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা ও অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা রক্ষা করা।
ভবিষ্যতে যারা জিও-পলিটিকসের শিকার হতে পারে:
আগামী দিনে জিও-পলিটিকসের শিকার হবে সেইসব দেশ যারা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, অথচ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বা নিরপেক্ষ অবস্থান রক্ষা করতে ব্যর্থ। যদি কি-না পররাষ্ট্রনীতিতে ভারসাম্য রাখে, অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখে ও বহুমুখী কূটনীতির (multivector diplomacy) চর্চা করে তাহলে তারা জিও-পলিটিক্যাল শিকার নয়, বরং চতুর খেলোয়াড় হয়েও উঠতে পারে। তবে আরও কিছু দেশ জিও-পলিটিকসের শিকার হতে পারে। যেমন:
তাইওয়ান:
চীন বারবার তাইওয়ানকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করে, আবার আমেরিকা তাকে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা দেয়। কারণ: দক্ষিণ চীন সাগরে সামরিক আধিপত্য, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণ (TSMC). এতে চীন-আমেরিকার সংঘাতে যেকোনো সময় যুদ্ধ হতে পারে।
পাকিস্তান:
চীনের সাথে অতি ঘনিষ্ঠতা, ভারতের সঙ্গে সংঘাত, আফগানিস্তান ও ইরানের পাশে হওয়ায় দেশটির ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া CPEC প্রকল্প (চীন-পাকিস্তান করিডোর), চীন-ভারত প্রতিযোগিতা, কাশ্মীর ইস্যুসহ ইত্যকার কারণে দেশটির অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং বড় শক্তির সামরিক-অর্থনৈতিক খেলায় ব্যবহৃত হতে পারে।
ইথিওপিয়া:
জল ও জাতিগোষ্ঠী কেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বীয় দ্বন্দ্বের ঝুঁকি রয়েছে। কারণ: নীলনদ নিয়ে ইথিওপিয়া-সুদান-মিসরের ত্রিমুখী জলসংকট, জাতিগত সংঘাত (Tigray), চীনা বিনিয়োগ বনাম পশ্চিমা চাপসহ জলবায়ু ও জলের জিও-পলিটিকস বিদ্যমান।
নাইজার-সাহেল অঞ্চল:
ফ্রান্স, রাশিয়া ও পশ্চিমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবের ঝুঁকি রয়েছে। কারণ: ইউরেনিয়াম-তেল, সামরিক অভ্যুত্থান ও ইসলামি জঙ্গিবাদ, পশ্চিমা সামরিক উপস্থিতি এবং ‘নিও-কলোনিয়ালিজম’ বা প্রতিস্থাপনমূলক সাম্রাজ্যবাদ।
ইউরোপের বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ (লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া):
রাশিয়ার ভয় এবং ন্যাটোর উপস্থিতির ঝুঁকি রয়েছে। কারণ: ন্যাটো বনাম রাশিয়ার সামরিক দণ্ডায়মানতা, কৌশলগত অবস্থান (রাশিয়ার কালিনিনগ্রাদ অঞ্চল কাছাকাছি)। যাতে রাশিয়ার আগ্রাসনের সম্ভাব্য পরবর্তী লক্ষণ বিদ্যমান
ল্যাটিন আমেরিকার ভেনেজুয়েলা:
মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও চীনা-রুশ সমর্থনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ: বিশাল তেলের মজুদ, সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে পশ্চিমা বিরোধিতা এবং দুর্বল অর্থনীতি ও পরাশক্তির চাপ।
দ্বীপ রাষ্ট্র ও প্রশান্ত অঞ্চল:
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সামুদ্রিক আধিপত্যবাদের ঝুঁকি রয়েছে। কারণ: সামরিক ঘাঁটি স্থাপন ইস্যু, জলবায়ু বিপর্যয় ও সহায়তার নামে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।