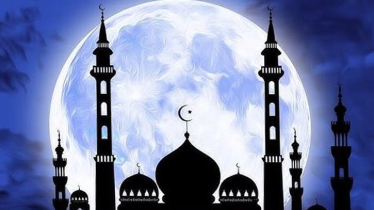ভারত–চীন সম্পর্কের আকৃতি এখন যুক্তরাষ্ট্রকে এক জটিল কৌশলগত ম্যাট্রিক্সে ফেলে দিয়েছে। একদিকে এশিয়ার দুই দৈত্যের প্রতিযোগিতা—সীমান্ত, সামুদ্রিক আধিপত্য, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যের অঘোষিত ঠান্ডা যুদ্ধ—অন্যদিকে তাদের পরস্পর-নির্ভর অর্থনীতি ও আঞ্চলিক প্রাতিষ্ঠানিক জোট (ব্রিকস, এসসিও)–এ নৈকট্য। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এর অর্থ—ইন্দো-প্যাসিফিক জুড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামাল দিতে দিতে এমন এক অংশীদার (ভারত)–কে ধরে রাখা, যে একযোগে প্রতিরোধ ও ‘স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি’—দুটোই চায়; এবং এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বী (চীন)–কে ঠেকানো, যে মার্কেন্টাইল ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতায় এখনও অনেকাংশে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের কেন্দ্রে।
প্রথমত, সামরিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্তরে ভারত–চীন সম্পর্কের যে কোনও উত্থান–পতন যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি চাপে ফেলে। সীমান্তে উত্তেজনা বাড়লে ভারত ওয়াশিংটনের দিকে আরও ঝুঁকে পড়ে—ইন্টেল শেয়ারিং, উচ্চ–উৎপাদন ক্ষমতার আর্টিলারি, ড্রোন, সমুদ্রসচেতনতা (MDA) ও লজিস্টিক্সে সহায়তা চায়—এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা–শিল্পভিত্তিকে দুই ফ্রন্টে (ইউরোপ–ইউক্রেন ও ইন্দো–প্যাসিফিক) একসঙ্গে টান পড়ে। বিপরীতে, যদি দিল্লি–বেইজিং একটি কার্যকর ডি-এস্কেলেশন বা সীমিত সমঝোতায় আসে, তাহলে কোয়াডের কৌশলগত গতি কমে যেতে পারে; ওয়াশিংটনের ‘চায়না-ব্যালান্সিং’ ন্যারেটিভ দুর্বল হয়; দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন প্রভাব–ক্রেডিটও কিছুটা ক্ষয় হয়। অর্থাৎ, সংঘর্ষ হোক বা আপস—দুই পরিস্থিতিই যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আলাদা ধরণের চাপ সৃষ্টি করে।
দ্বিতীয়ত, অর্থনীতি ও প্রযুক্তির ফ্রন্টে ভারত–চীন প্রতিযোগিতা যুক্তরাষ্ট্রের ‘ডি-রিস্কিং’ প্রকল্পের জন্য একইসাথে সুযোগ ও ঝুঁকি। চীনের উপর প্রযুক্তি–নিয়ন্ত্রণ (সেমিকন্ডাক্টর, এআই, ডুয়াল–ইউজ) জোরদার হলে ভারত ‘চায়না+১’ হিসেবে ম্যানুফ্যাকচারিং ও প্যাকেজিং–টেস্টিং–অ্যাসেম্বলির বড় অংশ টানতে পারে—কিন্তু দিল্লি যদি বাজার–অ্যাক্সেস, ডেটা–লোকালাইজেশন, শুল্ক–বাধা ও আইপিআর–ঝুঁকি কমাতে দ্রুত সংস্কার না করে, তবে কর্পোরেট আমেরিকার ‘রিরাউটিং’ অর্ধেক পথেই থমকে যাবে। আবার ভারত–চীন বাণিজ্যিক নির্ভরতা (ভারতের ফার্মা–ইলেকট্রনিক্স ইন্টারমিডিয়েটস) হঠাৎ ছিন্ন হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কোম্পানিও সেকেন্ড–অর্ডার শক খাবে—মূল্যস্ফীতি, লিড–টাইম, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাড়বে।
তৃতীয়ত, রিজিওনাল আর্কিটেকচারে দিল্লির ‘নন–অ্যালাইড অথ প্রো–ওয়েস্ট’ ভঙ্গি—ব্রিকস বিস্তার, রাশিয়া–সঙ্গত তেল–আমদানি, এবং একইসাথে কোয়াড–ভিত্তিক সমুদ্র–সহযোগিতা—ওয়াশিংটনের জন্য এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য–খেলা। মানবাধিকার, গণতন্ত্র–মাপকাঠি, ভিসা/ডায়াসপোরা–রাজনীতি—এসব ইস্যুতে অতিরিক্ত চাপ ভারতকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘স্ট্র্যাটেজিক স্পেস’ বাড়াতে প্রলুব্ধ করতে পারে, যেখানে চীন অর্থ–অবকাঠামো–বাজার–লেভারেজ দিয়ে নিজের জায়গা বানায়।
এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী করণীয় কী হতে পারে—তার একটি বাস্তববাদী, ধাপে–ধাপে নকশা নিচে দেওয়া হলো, যেখানে উদ্দেশ্য হল চীনা প্রভাবকে ভারসাম্য করা, ভারতীয় স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করা, এবং সিস্টেমিক ঝুঁকি না বাড়িয়ে সক্ষমতা–নির্মাণ করা।
প্রথমত, ‘ডিটারেন্স বাই ডেনায়েল’–ভিত্তিক সমুদ্র–কৌশলকে ভারত–মুখী করা। আন্দামান–নিকোবর–মালাক্কা আর্কে সামুদ্রিক ডোমেইন–সচেতনতা, সাবসারফেস ট্র্যাকিং, অ্যান্টি–সাবমেরিন ও আনম্যানড সারফেস/সাবসারফেস সিস্টেমে যৌথ সক্ষমতা বাড়ানো; LEMOA–COMCASA–BECA–র ব্যবহারকে অপারেশনাল রুটিনে নামিয়ে আনা; মেরিটাইম ‘কুইক–রিপেয়ার/রিপ্লেনিশ’ হাব হিসেবে ভারতীয় শিপইয়ার্ড–বন্দরকে নিয়মিত করা। এতে LAC উত্তেজনা হোক বা না–হোক, সমুদ্রপথে চীনা কনভয়/গ্রে–জোন কৌশলের খরচ বাড়ে।
দ্বিতীয়ত, ‘কো–ডেভেলপ, কো–প্রডিউস, কো–মেনটেইন’—এই ত্রিমাত্রায় প্রতিরক্ষা–শিল্প সংযুক্তি। জেট–ইঞ্জিন, মুণ্ডিত–ড্রোন, কাউন্টার–UAS, আর্টিলারি–প্রপেল্যান্ট, রেডিও–ফ্রিকোয়েন্সি ও ইলেক্ট্রনিক–ওয়ারফেয়ার—যেখানে ভারতীয় মেক–ইন–ইন্ডিয়া বাসনা মেলে, সেখানে ট্রান্সফার–অফ–টেক ও সোর্সিং–ডাইভারসিটি—দুটোকেই প্রাধান্য। লক্ষ্য হবে—ভারত দ্রুত স্কেল–আপ করতে পারুক, আবার যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্লাই–চেইনও আরও স্থিতিস্থাপক হোক।
তৃতীয়ত, প্রযুক্তি–রুলসের ‘গার্ডরেল’ রেখে বাজার–অ্যাক্সেসে বাস্তব সুবিধা। সেমিকন্ডাক্টর–প্যাকেজিং, পাওয়ার–ইলেকট্রনিক্স, টেলিকম–অবকাঠামো (ওপেন–RAN), ক্লাউড–ডাটা–সেন্টার, স্যাটকম—এই সেক্টরে মার্কিন–ভারত যৌথ ইনভেস্টমেন্ট–ফ্রেমওয়ার্ক, দ্রুত ভিসা/ট্যালেন্ট–মোবিলিটি, এবং ডেটা–ট্রান্সফার–নর্মসের কার্যকর সমঝোতা। লক্ষ্য—চীন–কেন্দ্রিক ডিপ–সাপ্লাই ব্যতীত ভারতকে ‘সিস্টেম–ইন্টিগ্রেটর’ হিসেবে দাঁড় করানো, তবে ডুয়াল–ইউজ–লিকেজ ঠেকাতে এক্সপোর্ট–কন্ট্রোল–কমপ্লায়েন্সে যৌথ সেল গড়া।
চতুর্থত, ‘ক্রাইসিস মেকানিক্স’ তৈরি—যৌথ পরিস্থিতি–ঘড়ি। LAC–এ আকস্মিক উসকানি বা দক্ষিণ চীন সাগরে গ্রে–জোন সংঘাতে কো–অর্ডিনেটেড রুলস–অফ–এনগেজমেন্ট, রিয়েল–টাইম হটলাইন, এবং ট্রায়াঙ্গুলার ডি–কনফ্লিকশন (যুক্তরাষ্ট্র–ভারত–জাপান/অস্ট্রেলিয়া)–এর প্রটোকল আগে থেকে মহড়া দেওয়া। এতে ভুল–বুঝাবুঝির জানালা ছোট হয়, এসক্যালেশন–ল্যাডার নিয়ন্ত্রণে থাকে।
পঞ্চমত, অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনীতি—ক্রিটিক্যাল মিনারেলস থেকে সাপ্লাই–চেইন ফাইন্যান্স। লিথিয়াম–কোবাল্ট–নিকেল–গ্রাফাইটে ভারত–অস্ট্রেলিয়া–ইন্দো–প্যাসিফিক করিডর, এক্সপোর্ট–ইনশুরেন্স/ডিএফসি–ফাইন্যান্সিং দিয়ে ভারতীয় প্রোসেসিং–ক্যাপাসিটি তোলা; ফার্মা–অ্যাক্টিভ–ইন্টারমিডিয়েটস ও ইলেকট্রনিক্স–কম্পোনেন্টে ‘বাই–ডাউন রিস্ক’ স্কিম, যাতে মার্কিন ক্রেতার ট্রানজিশন–কস্ট কমে। লক্ষ্য—চীনা একচেটিয়া সাপ্লাইয়ের উপর নির্ভরতা ধীরে কমিয়ে প্রতিস্থাপকতা বাড়ানো।
ষষ্ঠত, আঞ্চলিক রাজনীতিতে ‘নো–ফোর্সড চয়েস’–নীতির প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি। ভারতকে কোনও ব্লকে বেঁধে না রেখে ইস্যু–ভিত্তিক কোলিশনে জায়গা দেওয়া—মানবাধিকার বা গণতান্ত্রিক মান–দাবিতে টোন–ডাউন কিন্তু টার্গেটেড—যাতে রিভার্বারেশন কূটনীতিতে নয়, প্রকল্প–অ্যাক্সেসে পড়ে। এতে দিল্লি–বেইজিং নৈকট্য যদি ট্যাকটিক্যাল হয়, তা স্ট্র্যাটেজিক হয়ে উঠতে কম প্রণোদনা পায়।
সপ্তমত, ইনফরমেশন–অ্যাকশন—ভুল–তথ্য, ফ্রন্ট–নেটওয়ার্ক ও শ্যাডো–ফাইন্যান্সে যৌথ নজরদারি। সীমান্ত–সংকট বা নির্বাচনী মৌসুমে সোশ্যাল–ইনফ্লুয়েন্স অপারেশনের বিপরীতে টেকনিক্যাল সাপোর্ট, প্ল্যাটফর্ম–কো–অপারেশন ও লিগ্যাল–অ্যাসিস্ট্যান্স—কিন্তু সার্বভৌমত্ব–সংবেদনশীলতা মাথায় রেখে। লক্ষ্য—চীনা ন্যারেটিভ–অ্যাডভান্টেজ কমানো, ভারতীয় জনমত–ব্যাকল্যাশ এড়ানো।
অষ্টমত, কূটনীতি–অর্থনীতি–প্রতিরক্ষা—এই তিনে ‘থ্রেডিং দ্য নিডল’। রাশিয়া–ফ্যাক্টর বা গ্লোবাল সাউথ–রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র যদি ভারতের ‘হেজিং’–কে নরম–চোখে দেখে, দিল্লি পাল্টা এশিয়ার মেরিটাইম সিকিউরিটিতে আরও প্রকাশ্য দায়িত্ব নিতে পারে। এতে ভারত–চীন ‘ঠান্ডা’ থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের ডিটারেন্স–ইকোসিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।
শেষ কথা—ভারত–চীন সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রকে চাপে ফেলবে কি না—এর উত্তর ‘হ্যাঁ, তবে নিয়ন্ত্রিতভাবে ফেলতে পারে’। কারণ যে–কোনও দিকেই দোল খেলে ওয়াশিংটনকে অতিরিক্ত সক্ষমতা, অতিরিক্ত সমন্বয় ও অতিরিক্ত রাজনৈতিক পুঁজি খরচ করতে হয়। সমাধান একটাই—একটি ‘ডুয়াল–ট্র্যাক’ কৌশল: চীন–নিরুৎসাহনে কঠিন, ভারতের স্ট্র্যাটেজিক অটোনমিকে সম্মানে নরম; সমুদ্র–নিরাপত্তায় অপারেশনাল, প্রযুক্তি–শাসনে গার্ডরেলড; অর্থনীতিতে বাজার–উন্মুক্ত কিন্তু ঝুঁকি–পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়িত। এতে কোয়াডের গতি অটুট থাকে, দিল্লির স্বায়ত্তশাসনও অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং যুক্তরাষ্ট্র—ইউরোপ–এশিয়া—দুই থিয়েটারেই দীর্ঘখেলা চালাতে পারে।