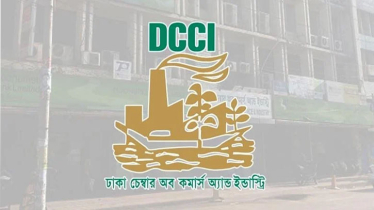বিশ্ব রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও বৈদেশিক নীতি নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থান পুনরায় আলোচনায় এসেছে। ট্রাম্পের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন বা রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন নীতির প্রভাব এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভূরাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠেছে—চীন ও ভারত কি কোনোভাবে এই ইস্যুতে পারস্পরিক স্বার্থে এক হতে পারে? নইলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ায় সাত বছর পর প্রথমবারের মতো চীন সফরে কেনো যাচ্ছেন ভারতের মোদি ?
ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে আমেরিকার ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতি বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্র দুই দিকেই বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। চীনের বিরুদ্ধে শুল্ক বৃদ্ধি, প্রযুক্তি কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং দক্ষিণ চীন সাগর ইস্যুতে মার্কিন অবস্থান দুই দেশের সম্পর্ককে প্রায় শীতলযুদ্ধে পরিণত করেছিল। অন্যদিকে, ভারতের ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসন একদিকে প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব বাড়ালেও, বাণিজ্য ও ভিসা নীতিতে কিছুটা চাপ সৃষ্টি করেছিল। ফলে, উভয় দেশই ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি থেকে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ—দুই ধরনের অভিজ্ঞতা পেয়েছে।
চীনের ক্ষেত্রে, ট্রাম্পের কঠোর বাণিজ্য যুদ্ধ ও প্রযুক্তি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কৌশল বেইজিংকে আরও আত্মনির্ভরতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। ভারতও একই সময়ে মার্কিন বাজারে শুল্ক সংক্রান্ত বিরোধ, জেনারেলাইজড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স (GSP) সুবিধা প্রত্যাহার এবং অভিবাসন ভিসা কঠোরতার মুখে পড়ে। যদিও নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় আমেরিকা ভারতের ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হয়, তবুও বাণিজ্য ক্ষেত্রে কিছু অসন্তোষ থেকে যায়। এখন, যদি ট্রাম্প পুনরায় ক্ষমতায় আসেন, তবে চীন ও ভারত উভয়ের সামনে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ব্যবস্থাপনায় নতুন সমীকরণ তৈরি হবে। সম্ভাব্য মিল হতে পারে সেইসব ক্ষেত্র, যেখানে মার্কিন নীতি তাদের অভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে—যেমন শুল্ক বৃদ্ধি, প্রযুক্তি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, কিংবা বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টি। তবে এই সম্ভাব্য মিল রাজনৈতিক জোটে রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা সীমিত, কারণ চীন-ভারতের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রতিযোগিতা এবং আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের দ্বন্দ্ব গভীর। তাছাড়া বাংলাদেশের ডেইলি স্টার পত্রিকা লিখেছে-হিন্দি-চীনী ভাই ভাই'—স্লোগানটি বললেই মনে ভাসে সদ্য স্বাধীন ভারত তথা মধ্য ১৯৫০ এর দশক ও এর প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কথা। মনে আসে ১৯৫৪ সালে অক্টোবরে নেহরুর সেই সময়ের পিকিং বা বর্তমানের বেইজিং সফরের ঘটনাপ্রবাহ। ইতিহাস বলছে—সেসময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে তুং সফররত নেহরুকে বলেছিলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দুই দেশকে (চীন ও ভারত) পরাশক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায় না।' প্রায় ৭০ বছর পর একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে যাচ্ছে কি?
সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে এতে আরও বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বেইজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চাঙা হওয়ার সুযোগ এসেছে।নয়াদিল্লি ও বেইজিংয়ের বর্তমান সম্পর্কের ওপর দৃষ্টিপাত করার আগে বলে রাখা দরকার যে, ১৯৬২ সালে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে প্রতিবেশী চীনের কাছে হেরে যাওয়ার পর সেই 'হিন্দি-চীনী ভাই ভাই' স্লোগানটি 'হারিয়ে' যায় বললে অত্যুক্তি হবে না। কেননা, সেই যুদ্ধের পর হিমালয়ের দুই পাশের দুই প্রতিবেশী ভারত ও চীন পরস্পরকে শত্রু ভাবতে শুরু করে।হালে শুল্কযুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের চক্ষুশূল হওয়ায় নয়াদিল্লি ও বেইজিং আবারও নিজেদের 'ভাই' ভাবতে শুরু করে কিনা তাই এখন দেখার বিষয়।
তবে এক ধরনের ‘প্রয়োজনভিত্তিক সমঝোতা’ অস্বীকার করা যায় না—যেমন ব্রিকস বা সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার মতো বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্মে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে এক ধরনের কৌশলগত সমন্বয়। এর উদ্দেশ্য হবে সরাসরি মিত্রতা নয়, বরং স্বার্থ রক্ষায় ন্যূনতম সমঝোতা গড়ে তোলা। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এই ধরনের ‘ইস্যুভিত্তিক সহযোগিতা’ নতুন কিছু নয়, এবং মার্কিন নীতি যদি উভয় দেশের অর্থনৈতিক বা কৌশলগত স্বার্থে একসাথে চাপ সৃষ্টি করে, তবে এটি আরও তীব্র হতে পারে। অতএব, আমেরিকা তথা ট্রাম্প ইস্যুতে চীন ও ভারতের এক হওয়ার সম্ভাবনা সরাসরি রাজনৈতিক জোটে নয়, বরং সীমিত পরিসরে, নির্দিষ্ট বিষয়ে সমন্বিত অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে—যেখানে দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্বকে সাময়িকভাবে উপেক্ষা করে কৌশলগত বাস্তবতা প্রাধান্য পাবে।